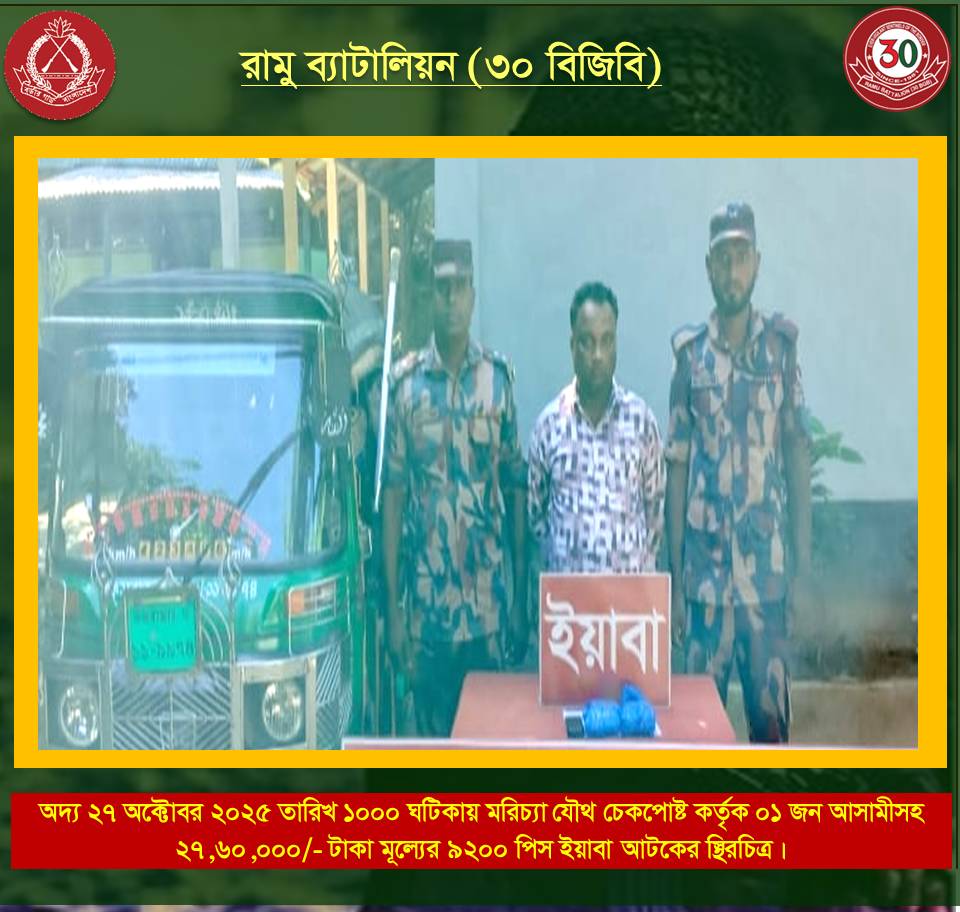এখনও উপেক্ষিত মাতৃভাষা বাংলা

- আপডেট সময় : ৪৩৯ বার পড়া হয়েছে
বছর ঘুরে আবার এলো ফেব্রুয়ারি। বাঙালির জীবনে এই মাসের পরিচিতি ‘ভাষার মাস’ হিসেবে। ১৯৫২ সালের প্রথম ভাগ থেকে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলন ছিল, উর্দু নয়, বাংলাই হবে এ দেশের রাষ্ট্রভাষা। ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আন্দোলনে গুলি চালালে শহীদ হন রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ অনেকে। এই আন্দোলনের মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা ভাষা পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও। সেই আন্দোলনেরও পেরিয়ে গেছে ৭২ বছর, কয়েক দিন পর ৭৩ পূর্ণ হওয়ার পথে। আর স্বাধীনতার পর পেরিয়ে গেছে ৫৩ বছর। এত এত বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও দেশে হয়নি ভাষানীতি। এ ছাড়া সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার এখনও উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। শুধু বাংলাই নয়, হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষাগুলোও। অফিস-আদালত-ব্যাংকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ও বাংলা ভাষা একই সঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার জায়গায় গুরুত্ব পাচ্ছে ইংরেজি ও আরবি ভাষা। একই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাগুলোও। কোনো সরকারই এখন পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি।
ভাষা নিয়ে এই উদাসীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভাষাসংগ্রামী ও শিক্ষাবিদরাও। তারা মনে করেন, এভাবে চলতে থাকলে হারিয়ে যাবে মাতৃভাষাগুলো। ভাষানীতি প্রণয়ন না করলে ভাষাগুলোকে রক্ষা করা যাবে না। এ ছাড় নিশ্চিত করতে হবে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা। ভাষার যত্ন নেওয়া না হলে হারিয়ে যাবে ভাষা। ইউনেস্কো বলছে, ইতোমধ্যে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়ার ভাষার সঠিক হিসাব তাদেরও জানা নেই।
বিশ্বে ভাষার ব্যবহারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা এথনোলগ বলছে, পৃথিবীতে বর্তমানে ৭ হাজার ১৬৮টি ভাষা রয়েছে। কিন্তু এর ৪২ শতাংশই ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ অবস্থায় আছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ভাষা চিরতরে হারিয়েও গেছে। তবে যেসব ভাষা পৃথিবীতে এখনও বহাল তবিয়তে টিকে আছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইংরেজি বা ইংলিশ। পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েকটি দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি; কিন্তু পৃথিবীতে এমন দেশ বিরল যেখানে মাতৃভাষার পর ইংরেজিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ৮০০ কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি মানুষই ইংরেজিতে কথা বলে। এথনোলগের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৭ কোটির কিছুটা বেশি। পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত ভাষাগুলোর মাঝে বাংলা সপ্তম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বসবাস বাংলাদেশে, এরপর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী বলেন, আমাদের নৈতিকতা দরকার। বাংলা ভাষাটাকে নিজের মনে করতে হবে। নিজের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্য আছে। আমাদের এই ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা কতটুকু? আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ বাইরের দেশে থিতু হওয়ার চিন্তা করে। তারা একরকম পাশ্চাত্যমুখী। তাই ইংরেজি ভাষাকে অগ্রাধিকার দেয়। চীন দেশের মানুষদের নিজের ভাষা নিয়ে কোনো হীনমন্যতা নেই। তারা তাদের চাইনিজ ল্যাংগুয়েজকে বাইরেও ছড়িয়ে দিচ্ছে, নিজেরা এসে শেখাচ্ছেও। আমাদেরও উচিত বাংলা ভাষাকে ভালো করে আয়ত্ত করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। সেজন্য বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকে গুরুত্ব দিতে হবে। জানতে হবে, চর্চা করতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, এখন বলা হয় ইংরেজি শেখ, একটা সময় ফারসি শেখানো হতো। এটা একটা ক্ষমতার চর্চা, উপনিবেশবাদ। উন্নত জাতি অনুন্নত জাতিকে ভাষার মাধ্যমে দমাতে পারে। বাংলা যেমন আমাদের রাষ্ট্র ভাষা। যেকোনো দেশে একটা সাধারণ ভাষা থাকা প্রয়োজন, যাতে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আমরা যেমন ইংরেজি ভাষায় পিষ্ট হচ্ছি, তেমনি আমাদের আদিবাসীদের ভাষাগুলোও যেন বাংলা ভাষার চাপে না পড়ে যায়, তাদের মাতৃভাষাকেও রক্ষা করতে হবে। সেজন্য বড় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে এজন্য কাজ করতে হবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও প্রয়োজন। আর এজন্যই ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।’
এদিকে বাংলাদেশ সরকার ২০১৯ সালে ৫০টি নৃ-জাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসত্তা আছে কিন্তু ভাষা হারিয়ে গেছেÑ এমন ১৫টি ভাষার বিপন্নতার কথা জানায় আন্তর্জাতিক সংস্থা সামার ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকস (সিল)। সংস্থাটি বলছে, এসব জাতিসত্তার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থান দুর্বল। জীবন-জীবিকার তাগিদে ছুটতে গিয়ে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও নিজস্বতার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তাদের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা মাতৃভাষা শেখার বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা স্থানান্তরের প্রতি অনীহা তৈরি করছে। এসব জাতিগোষ্ঠী হলোÑ কন্দ, গঞ্জু, বানাই, বাড়াইক, বাগদি, ভূমিজ, খাড়িয়া, মালো, মুসহর, তেলি, তুরি, রাজোয়ার, হুদি, পাত্র ও ভুঁইমালী।
এদের মধ্যে মালো, বাড়াইক ও গঞ্জু সম্প্রদায়ের লোকেরা মৌখিকভাবে ‘সাদরি’ ভাষা ব্যবহার করে। তবে এ ভাষার কোনো লিপি নেই। তেলি সম্প্রদায়ের ভাষা ‘নাগরি’, তুরি সম্প্রদায়ের ‘খট্টা’, মুসহর সম্প্রদায়ের ‘দেশওয়ালি’ ও ‘নাগরি’, কন্দ সম্প্রদায়ের ‘কুই’ ও ‘উড়িয়া’ ভাষা হুমকির সম্মুখীন। পাত্র সম্প্রদায় ‘লালেংথার’ এবং বানাই সম্প্রদায় ‘বানাই’ ভাষায় এখনও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে। রাজোয়ার সম্প্রদায়ের ‘খট্টালি’ আর খাড়িয়া সম্প্রদায়ের ‘ফারসি’ ভাষা। মৃতপ্রায় ভাষার মধ্যে আছে বাগদি, হুদি ও ভুঁইমালী। এই সম্প্রদায়গুলোর ভাষার মৌখিক প্রচলন নেই, লিখিত তথ্যও পাওয়া যায়নি।
নিজের ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে লড়াই করে যাচ্ছে নৃগোষ্ঠী জাতিগুলোও। ভাষাভাষীদের দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশে বাংলার পরেই চাকমা ভাষার অবস্থান। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, চাকমা জনগোষ্ঠী ৪ লাখ ৪৪ হাজার। তাদের ভাষার নিজস্ব বর্ণমালাও রয়েছে। কিন্তু এই ভাষার চর্চাও হচ্ছে না যথাযথভাবে।
নৃ-গোষ্ঠীদের বহুল ব্যবহৃত ভাষাটিও বিলুপ্তির পথে মনে করেন সুজন চাকমা। নিজের ভাষার বর্ণমালা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনলাইন ও অফলাইনে এই ভাষার বর্ণমালা শেখাচ্ছেন তিনি। সুজন বলেন, ‘অনেকেই মনে করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ ভাষার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই বলতে পারলেও কেউ এ ভাষার বর্ণমালার চর্চা করে না। যখন তৃতীয় শ্রেণি বা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তাম, তখন স্কুলে প্রশ্নে এসেছিলÑ মাতৃভাষা কী? পরীক্ষায় নম্বর পেতে উত্তর দিয়েছিলামÑ বাংলা। তবে এতে বেশ খারাপ লেগেছিল। পরে ২০১৩ সালে একজন বৈদ্য যাদের তান্ত্রিক বলা হয়, যিনি মন্ত্র পড়েন, তাকে দেখলাম এ বর্ণমালা লিখতে পারেন। তবে তা শুধু মন্ত্র পড়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। এ বর্ণমালায় কোনো বইও সহজলভ্য ছিল না শেখার জন্য। ২০১৭ সালে চাকমা বর্ণমালা শিখি, এখন অনলাইন ও অফলাইনে অন্যদের শেখাই, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে সচেতন করি।’
তেমনই একজন যুবরাজ দেববর্মা। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করেছেন তিনি। শ্রীমঙ্গলের ডলুছড়ার এই ত্রিপুরা তরুণ তার মাতৃভাষা ‘ককবরক’ বইটি অনুবাদ করেছেন। ত্রিপুরাদের ভাষা আছে, কিন্তু তার লিখিত রূপ দিতে নেই বর্ণমালা। ফলে ভাষা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এই তরুণ বলেন, ‘‘ভারতীয় উপমহাদেশে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ, আমাদের ভাষাও তাই। কিন্তু কম মানুষের ভাষা হওয়ায় চর্চাও কম। তাই ‘ককবরক’-কে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি।’’
এমন আরও সম্প্রদায় নিজের মাতৃভাষাকে টিকিয়ে রাখতে এগিয়ে আসছে। এবার আসা যাক কড়া সম্প্রদায়ের দিকে। একদিকে তারা সংখ্যায় কম, শিক্ষায়ও পিছিয়ে, তাই নিজ জাতিগোষ্ঠীকে শিক্ষায় এগিয়ে নিতে নিজ গ্রামেই পাঠশালা গড়ে তুলেছেন লাপোল কড়া নামে এক তরুণ। যেখানে তার নিজের ভাষা সাদরিতেই শিশুদের পড়া বুঝিয়ে দেন তিনি। লাপোল কড়া বলেন, ‘মায়ের পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কিছু জমি ছিল। বাবাও দিনমজুরি করতেন। ফলে কোনোমতে দুবেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু খেটে খাওয়া পরিবারগুলো কীভাবে তাদের সন্তানদের শিক্ষার খরচ জোগাবে, তাই স্কুলে ভাষার সংকটে পড়ে অনেকেই স্কুলমুখী হতে চাইত না। কড়া পাঠশালায় দুজন ওঁরাও শিক্ষকও সাদরি ভাষায় কথা বলেন। আমি এখন স্বপ্ন দেখছি, আমাদের আর কোনো ভাইবোন ভাষাগত সমস্যার কারণে স্কুল ছাড়বে না।
মাতৃভাষা ব্যবহারে রাষ্ট্রের উদাসীনতাকে দুঃখজনক বললেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘মাতৃভাষা ব্যবহারে দেশে এখন নীতিহীনতা চলছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। যেকোনো জাতিগোষ্ঠী প্রাথমিক স্তরে নিজ ভাষায় পড়াশোনা করবে। পরে ইংরেজি বা আরবিসহ অন্যান্য কিছু শিখবে। এটা নিয়ে একটা মডেল তৈরি করতে হবে। শুরুতেই অন্য ভাষা দরকার নেই। পরে সেই শিশু কোনো ভাষায় ভালো করতে পারবে না। নিজের ভাষায় শিশু পড়াশোনা করলে তার বিকাশ হবে। জ্ঞানের বিকাশ হবে।